প্রশ্নঃ আমার প্রশ্নটা ড. ইউনূসকে নিয়ে। একজন মানুষ যদি এত খারাপ কাজই করতেন, তিনি কি কখনো নোবেল পেতেন? তার সমালোচনা করাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত?
উত্তরঃ আসলে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই, কোনো ক্ষোভ নাই। আমাদের বক্তব্য একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে, তার প্রণীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে। এটা যদি মানুষের জন্যে কল্যাণকর হতো আমরা সবসময় তা সমর্থন করতাম। কিন্তু অকল্যাণকর হলে, যে যা-ই বলুক—তিনি যে স্তরেরই মানুষ হোন না কেন—আমরা সবসময় সেটার বিপক্ষে। ক্ষুদ্রঋণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে ইদানীং মিডিয়া হইচই করলেও এ ব্যাপারে আমরা কিন্তু বলে আসছি গত ২০ বছর ধরে।
সেদিন একটা খবর দেখলাম, জোবরা গ্রামের সুফিয়া, যিনি ঐ গ্রামের প্রথম ঋণ নেয়া মহিলা, তার ঘর নাকি এখন এত নড়বড়ে হয়ে গেছে যে, বর্ষাকালে তাকে অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হয়! যারা ডকুমেন্টারি নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন, তারাও ওখানে গিয়ে পাকা ঘর দেখেন নাই, জীর্ণ-শীর্ণ ঘর দেখেছেন। সুফিয়ার মতো অন্য ঋণগ্রহীতাদের প্রায় সবার মুখে একই কথা শুনেছেন। প্রত্যেকেই একাধিক ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং সেই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সবার প্রাণান্তকর অবস্থা—কেউ বাড়ি বিক্রি করেছেন, কেউ গরু বিক্রি করেছেন। আবার সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ করতে না পারায় কারো ঘরের টিন খুলে নিয়ে গেছে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এদের সাথে আগেকার দিনের গ্রাম্য মহাজনের কোনো তফাত নাই। এরা হচ্ছে আধুনিক স্যুট-প্যান্টধারী মহাজন।
ব্যাপারটা আমরা আরেকটু সহজভাবে দেখতে পারি। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে তিন লক্ষ সাত হাজার কোটি টাকা এসেছে ঋণ দেয়ার জন্যে। এই টাকাটা যদি আসলেই মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যয় করা হতো তাহলে আজকের অবস্থা কিন্তু এমন হতো না। ধরুন, এ টাকা দিয়ে যদি আমরা ১০০ কোটি টাকার একেকটা প্রকল্প করতাম তাহলে অন্তত তিন হাজার প্রকল্প হতে পারত। এবং প্রত্যেকটা উপজেলায় ১০টা করে প্রকল্প হতো এবং প্রত্যেক উপজেলায় এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারত।
এ বিনিয়োগ যদি কৃষিজ-বনজ-ফলজ খাতে ব্যয় হতো তাহলে আজকে তো গরিব লোকই খুঁজে পাওয়া যেত না! তখন শহরে আসার লোক কমে যেত। তারা ভাবত যে, গ্রামে যাই—ওখানে উপার্জন বেশি। অতএব যারা বিদেশ থেকে ঋণ পাঠায় তারা কখনোই আমাদের স্বাবলম্বী করার জন্যে ‘সাহায্য’ পাঠায় না। তারা ঋণ পাঠায় আমাদের গোলাম বানিয়ে রাখার জন্যে এবং ঐ টাকার ওপর মোটা অঙ্কের মুনাফা করার জন্যে।
ক্ষুদ্রঋণের বিড়ম্বনা নিয়ে ভাষাসৈনিক ও গবেষক আহমদ রফিক এক বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ লিখেছেন। এর অংশবিশেষ হচ্ছে-
কিছু বেসরকারি জরিপের সূত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমির মালিকানা মাত্র ১০ শতাংশ ধনী কৃষক বা ব্যবসায়ী অথবা কৃষক-ব্যবসায়ীর হাতে। আর ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা …. ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ। এ জনসংখ্যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ নারী, যারা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ঋণদান সংস্থার কাছে ছুটে যায়, বুঝে বা না বুঝে (গ্রামীণ বেওয়া)। তারপর যা ঘটার ঘটে।
এরাই ঋণ সংস্থার শিকারিদের ‘টার্গেট গ্রুপ’। কারণ এদের খুব সহজে সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখানো যায়, আর এদের কাছ থেকে জবরদস্তি সুদ আদায়ের কাজটা খুব সহজে করা যায়। সুদের টাকা দিতে না পারলে ছাগলটা কিংবা নিদেনপক্ষে হাঁসটা-মুরগিটা কব্জা করতে বা চালের টিন খুলে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। শক্ত হাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা এ অসহায় মহিলাদের নেই।
গ্রামের ঐ যে শক্তিমান ১০ শতাংশ মানুষ, তারাই গ্রামের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, গ্রামীণ সমাজ পরিচালনা করে থাকে। …. ঋণদান সংস্থাগুলো বুঝেশুনেই তাদের হাতে ঋণ বা ঋণের সুদ আদায়ের দায়িত্ব তুলে দেয়। ….
গ্রামীণ গরিবি দশা এতটাই প্রকট যে, ওই গরিবি ডোবায় ছিপ ফেলতে সবাই বেজায় আগ্রহী। ছোট একটা ঋণের ‘চার’ মুখের সামনে ধরলে ক্ষুধার্ত মাছ ধরা দেবেই। এরপর তাকে নিয়ে খেলান—যত বেশি খেলান যাবে তত বেশি লাভ। এ ঘটনা পুরনো কাবুলিওয়ালাদের কাহিনীর মতো—‘সুদ মাংতা, আসলি নেহি মাংতা’।
যে গরিব মানুষটিকে ঋণ নিতে হয়, চরম দারিদ্রের মুখে তার পক্ষে কি এক সপ্তাহের মধ্যে এমন লাভ সম্ভব যে, মূল টাকায় হাত না দিয়ে সে সপ্তাহান্তে সুদ পরিশোধ করতে পারে? …. ঋণ আদায়ের ভয়াবহতা এতটা বেশি যে, গরিব গ্রামীণ মানুষের জন্যে তা আর সেবার পর্যায়ে থাকে না, হয়ে ওঠে ঋণদাতার পক্ষে ব্যবসা তথা মুনাফাবাজি—আজকাল নানা তত্ত্বে এর নাম দেয়া হচ্ছে ‘সামাজিক ব্যবসা’।
স্বভাবতই জানা দরকার, কারা এ ধরনের প্রকল্পের ঋণদাতা, কী তাদের পরিচয়? দ্রুত গজিয়ে ওঠা ‘বেসরকারি সংস্থা’ তথা এনজিওগুলোই (যে নামে এ নব্য মহাজনদের সবাই চেনে, জানে) মূলত ওই ঋণদাতাগোষ্ঠী এবং তা ছোট-বড় নানা আকারের। ক্ষুদ্রঋণদাতা সংস্থা আকারে ক্ষুদ্র হলেও মুনাফার টানে ওই ক্ষুদ্রতা একসময় পাহাড়চূড়ায় উঠে যায়।
ক্ষুদ্র তখন আর ক্ষুদ্র থাকে না। লাভের পরিমাণ অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হয় এ ব্যবসায় বিত্তাকাঙ্ক্ষীরা লাইন দিয়ে নেমে পড়েছেন। বাংলাদেশ তাই কথিত এ সেবার শোষণ ব্যবসায়ের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট বাংলাদেশে এনজিও-র সংখ্যা কয়েক হাজার, কারো মতে ১৩ হাজার, কেউ লেখেন ২৫ হাজার। আর সুদের হার? সংস্থা থেকে সংস্থায় তা বিভিন্ন রকম। এক অর্থনীতিবিদের মতে, সুদের হার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ। ভাবা যায়! …..
এ আলোচনা দীর্ঘ হতে পারত। তবু ইতি টানছি একটি তথ্য দিয়ে। ক্ষুদ্রঋণ যদি গ্রামে দারিদ্রই দূর করবে, তাহলে এতগুলো বছর পর দরিদ্রের সংখ্যা শতাংশ হারে তো কমার কথা। কিন্তু কমছে না।
১৯৯৫ সালে বিআইডিএস-এর জরিপে দেখা যায়, ১৯৯৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দরিদ্র জনসংখ্যার হার ৪৮ শতাংশ এবং অতীব দরিদ্রের সংখ্যা ২৩ শতাংশ। ….
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের কাছ থেকে দিনকয় আগে জানা গেল, বেসরকারি জরিপে ২০০৫ সাল নাগাদ যে তথ্য, তাতে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ৪৮ শতাংশের মতো। [অর্থাৎ অতীব দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে ২৫ শতাংশ।]
সিদ্ধান্তটা তাহলে দাঁড়ায় : ক্ষুদ্রঋণ দানের মহাজনী ব্যবসা গ্রামীণ দারিদ্র নিরসনের বদলে দাতা সংস্থা-শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যই বিকশিত করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিত্তের পাহাড় সঞ্চয় এবং বহুমুখী বাণিজ্যের মুনাফায় আকাশচুম্বী। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের এমন পরিণাম তো প্রত্যাশিত হতে পারে না।
জনাব আহমেদ রফিকের পুরো বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রঋণ অতি দরিদ্রের সংখ্যা না কমিয়ে বাড়িয়েছে দ্বিগুণ। যেখানে ১৮ বছর আগে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ অতি দরিদ্র ছিল সেখানে এখন দেশের অর্ধেক মানুষই অতিদরিদ্র। ক্ষুদ্রঋণের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোর কাজের পরিণতি আসলেই খারাপ।
আরেকটা বিষয় হলো, আপনি যে নোবেল পুরস্কারের কথা বলছেন সেখানেও প্রকৃত সত্যটা কী? অনেক ক্ষেত্রেই শোষকরা যাকে তাদের স্বার্থের অনুকূলে মনে করে তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়। আর স্বার্থের প্রতিকূলে মনে করলে তাকে দেয় না। ধরুন, লিও টলস্টয়—যিনি এত বড় লেখক ছিলেন—তাকে শান্তিতে তো দূরে থাক, সাহিত্যেও নোবেল দেয়া হয় নি। অথচ নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হওয়ার ১০ বছর পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয় ১৯০১ সালে—টলস্টয় বেঁচে ছিলেন ১৯১০ পর্যন্ত। কেন দেয়া হয় নি? কারণ যারা পুরস্কার দেয়, টলস্টয়কে দিয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।
কাজেই নোবেল পুরস্কার যারা পান তাদের সব বক্তব্য ঠিক, সব কাজই ঠিক—এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। ড. ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে প্রথম যে কথাটি বললেন তা-ই ছিল ১৬ অক্টোবর, ২০০৬ সালের প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম—‘চট্টগ্রাম বন্দর মুক্ত করে দিন || দেশের চিত্র পাল্টে যাবে’। অর্থাৎ বিদেশিদের জন্যে বন্দর উন্মুক্ত করে দিলেই দেশের সব ভালো হয়ে যাবে।
নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি কীরকম বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাকে দেয়া সম্বর্ধনায়। ড. ইউনূস বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন নোবেল বিজয়ী দেশ। জাতি হিসেবে আমরা এখন অনেক ওপরে উঠে গেছি। হঠাৎ করে যেন আমরা প্রত্যেকে ১০ ফুট লম্বা হয়ে গেছি। বুকের ছাতি অনেক চওড়া হয়ে গেছে।’
একটা পুরস্কার পেয়ে মানুষ ১০ ফুট লম্বা কীভাবে হয়ে যায়? চিন্তা করুন, হিতাহিত জ্ঞান কতটা লোপ পেলে একজন মানুষ এমন কথা বলতে পারে! অবশ্য থলের বেড়াল বেরোতে সময় লাগে নি। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করলেন, রাজনৈতিক দল গঠন করবেন।
সাবেক সচিব কাজী ফজলুর রহমান তার রাজনীতিতে যোগদানের ঘোষণাকে আখ্যায়িত করেন ‘ড. ইউনূস || জোবরা থেকে গণভবন যাত্রা!’। অবশ্য এ ব্যাপারে তার আশাভঙ্গ হয়েছে খুব দ্রুত। অনেক বিশ্লেষকের মতে, তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেপথ্য চালকদের মাইনাস-২ ফরমুলা বাস্তবায়নের একটা ব্যর্থ উদ্যোগ ড. ইউনূস। ব্যক্তি ইউনূসের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। আমাদের বক্তব্য সামাজিক ব্যবসা নামক নব্য মহাজনী সুদি শোষণে নিজেরা ফুলে-ফেঁপে উঠে দরিদ্রকে ঋণচক্রে ফেলে আরো দরিদ্র সর্বস্বান্ত করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।












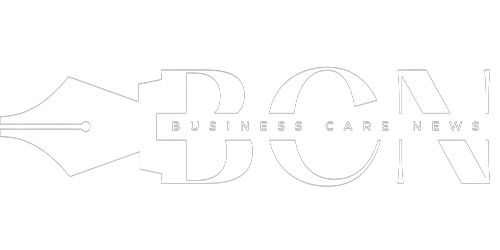
Related Posts
Q&A Series – Episode 292: Failure is the pillar of success!
Q&A Series – Episode 291: What exactly is visualization?
Q&A Series – Episode 290: How does visualization work?